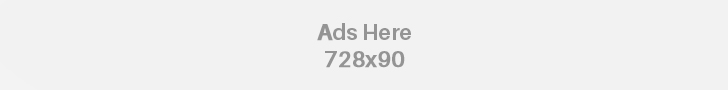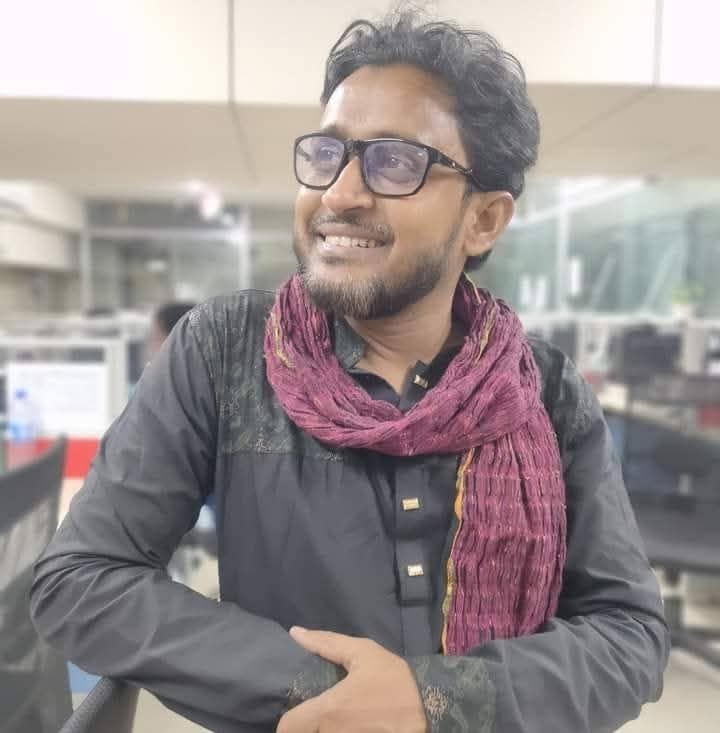আস্থার সঙ্কট থেকে সম্ভাবনার পথে

প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী চিকিৎসার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করেন। কেউ যান ভারতের চেন্নাই বা ভেলোরের বিশেষায়িত হাসপাতাল, কেউ সিঙ্গাপুরের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান, কেউবা ব্যাংককের নামকরা ক্লিনিক বা মালয়েশিয়ার প্রজনন চিকিৎসাকেন্দ্রে। রোগের ধরনও প্রায় একই। হৃদরোগ, কিডনি প্রতিস্থাপন, ক্যান্সারের জটিল চিকিৎসা, বন্ধ্যাত্বজনিত সমস্যা অথবা বড় ধরনের শল্যচিকিৎসা। এমনকি একটি নির্ভরযোগ্য ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার আশাতেও অনেক মানুষ বিদেশ যাত্রা করেন। এই বিদেশমুখী স্রোত শুধু চিকিৎসার খরচ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় না; বরং দেশের ভেতরে আস্থার ঘাটতি উৎকটভাবে প্রকাশ করে।
চিকিৎসার জন্য ভ্রমণ নতুন কোনো প্রবণতা নয়। প্রাচীন গ্রিসের কথা মনে করা যেতে পারে। মানুষ তখন এপিডাউরাসে আসক্লেপিওসের মন্দিরে যেত, যেখানে চিকিৎসা হতো এক ধরনের পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস একত্রে কাজ করত। সেই সময় থেকে মানুষ বুঝেছিল স্বাস্থ্য কেবল শরীরের অসুখ সারানো নয়; বরং মন, দেহ ও বিশ্বাসের সমন্বয়। রোমান যুগে চিকিৎসার ধারণা ছিল অন্যরকম। তারা বিশ্বাস করত উষ্ণ খনিজ বাথ ও প্রাকৃতিক ঝর্ণার আরামে। অসুস্থ মানুষদের জন্য আরোগ্য মানে ছিল যত্ন, আরাম এবং শরীরকে আরাম দেয়ার মতো পরিবেশ। আধুনিক ইউরোপ চিকিৎসার ধারণায় প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে যোগ করল। জার্মানির ব্যাডেন-ব্যাডেন কিংবা ইংল্যান্ডের বাথ শহর হয়ে উঠল সচ্ছল মানুষের জন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসা গন্তব্য। ফলে দেখা যায়, চিকিৎসা ভ্রমণের ইতিহাসে তিনটি ধাপ স্পষ্ট। গ্রিসে ছিল অবকাঠামো, রোমে ছিল যত্ন ও স্বাচ্ছন্দ্য, আর ইউরোপে যোগ হলো বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ। তিনটির মিলিত শক্তি চিকিৎসা ভ্রমণকে স্থায়ী ভিত্তি দিয়েছে।
বাংলাদেশের বাস্তবতায় সমস্যা হলো- আমরা স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নকে দীর্ঘদিন ধরে শুধু ইট-পাথরের অবকাঠামো নির্মাণে সীমাবদ্ধ রেখেছি। বড় বড় হাসপাতাল ভবন দাঁড় করানোকে উন্নয়নের প্রতীক ভাবা হয়েছে। অথচ স্বাস্থ্য হলো আস্থা, স্বাস্থ্য হলো যত্ন ও স্বাস্থ্য হলো প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার। নীতি প্রণয়ন ও বিনিয়োগে এই তিন দিক দীর্ঘদিন অবহেলিত থেকেছে। এর ফলে আধুনিক ডায়াগনস্টিক সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি অর্জনের উদ্যোগ যথাযথভাবে নেয়া হয়নি। রোগীদের জন্য সহজ নেভিগেশন বা পথনির্দেশের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। হাসপাতালের বিলিং প্রক্রিয়া আজো জটিল এবং অস্বচ্ছ। সবচেয়ে বড় ঘাটতি রয়েছে মানবিক যত্ন ও সহমর্মিতায়। চিকিৎসা কেবল ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের প্রক্রিয়া নয়। চিকিৎসা মানে, মানুষের সাথে মানুষের সংযোগ, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা। এ মৌলিক উপাদানকে নীতিগতভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়নি।
অন্যদিকে, অনেক দেশ সঙ্কটকে সুযোগে রূপান্তর করেছে। থাইল্যান্ড একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ভ্রমণ বিভাগ গড়ে তুলেছে। তারা নিশ্চিত করে যে, বিদেশী রোগী বিমানবন্দরে নামা থেকে শুরু করে চিকিৎসা সম্পন্ন হওয়া এবং বিদায় নেয়া পর্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা পান। ভারত জাতীয় চিকিৎসা ও সুস্থতা ভ্রমণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে, যা ভারতের স্বাস্থ্যসেবাকে বিশ্বজুড়ে প্রচার করে। তারা হাসপাতালগুলো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করেছে, চিকিৎসা প্রক্রিয়া সহজ করেছে এবং রোগীর অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মালয়েশিয়া স্বাস্থ্যসেবা ভ্রমণ কাউন্সিল তৈরি করেছে, যা সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বে রোগীবান্ধব অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে।
এসব দেশ প্রমাণ করেছে যে চিকিৎসা মানে কেবল হাসপাতালের শয্যা বা চিকিৎসকের দক্ষতা নয়। চিকিৎসা মানে- সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা, যেখানে রোগী বিশ্বাস করবেন- তিনি শুধু চিকিৎসা পাচ্ছেন না; বরং যত্ন ও মর্যাদা পাচ্ছেন।
বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো নাগরিকদের আস্থা ফিরিয়ে আনা। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বিশ্বাস না করবেন- নিজের দেশে নিরাপদ, আধুনিক ও মানবিক চিকিৎসা পাওয়া সম্ভব, ততক্ষণ বিদেশমুখী রোগীর স্রোত থামবে না। এ জন্য প্রয়োজন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। প্রথমত, উন্নত ডায়াগনস্টিক প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, এমন একটি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তৈরি করা যেখানে রোগী জানবেন কোথায় যেতে হবে, কীভাবে সেবা পাবেন এবং খরচ কত হবে। তৃতীয়ত, রোগীর সাথে আচরণে মানবিকতা ফিরিয়ে আনা। হাসিমুখ, স্পষ্ট যোগাযোগ ও আন্তরিক সহমর্মিতা দিয়ে আস্থা তৈরি করা সম্ভব। এ উপাদানগুলো অর্জন করতে বড় অঙ্কের অর্থ দরকার নেই; বরং দরকার সঠিক দিকনির্দেশনা, সুশাসন ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা।
কিন্তু এখানে থেমে গেলে চলবে না। বাংলাদেশকে আঞ্চলিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করার স্বপ্ন নিয়ে এগোতে হবে। আমাদের হাতে রয়েছে বেশ কিছু বিশেষ সুযোগ। তুলনামূলকভাবে খরচ কম, দক্ষিণ এশিয়ার রোগীদের সাথে সংস্কৃতিগত নৈকট্য, দক্ষ নার্সিং স্টাফ এবং ইংরেজিভাষী চিকিৎসক সমাজ। এগুলো কাজে লাগানো গেলে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার জন্য একটি বড় চিকিৎসা গন্তব্য হতে পারে। তবে এ জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে বিনিয়োগ। স্থানীয় গবেষণা ও আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে একটি বাংলাদেশ ব্র্যান্ড তৈরি করতে হবে। এই ব্র্যান্ড হবে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবিকতার সমন্বয়।
চিকিৎসা ভ্রমণ কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশ্ন নয়। এটি মানুষের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও বিশ্বাসের প্রশ্ন। একজন নাগরিক যদি মনে করেন কেবল আস্থার অভাবে তাকে বিদেশে যেতে হবে, সেটি একটি দেশের জন্য লজ্জাজনক। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রত্যেক বাংলাদেশীকে নিজের দেশে এমন চিকিৎসা দেয়া, যা দক্ষ, আধুনিক ও মানবিক। যদি আমরা এখনই নীতি ও বিনিয়োগের সঠিক দিক নির্ধারণ করি, তবে বিদেশমুখী রোগীর স্রোত ধীরে ধীরে কমে আসবে। আর একদিন হয়তো এমন সময় আসবে যখন বিদেশীরা চিকিৎসার জন্য আসবে বাংলাদেশে। তখন ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গ্রিস, রোম এবং ইউরোপের পর দক্ষিণ এশিয়ার চিকিৎসা মানচিত্রে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে এক নতুন কেন্দ্র।
লেখক: ডা: মো: রফিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, বিএনপি